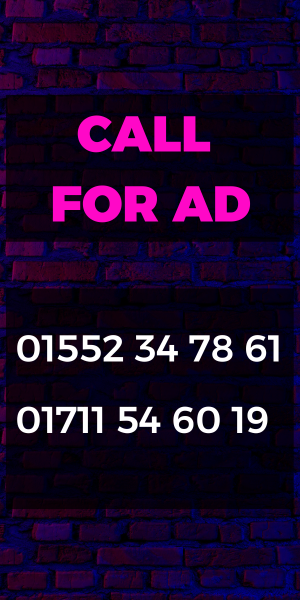প্রযুক্তির জোয়ারে মানুষ: অগ্রগতি নাকি পরাধীনতা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক মৃধা (সোহেল মৃধা): প্রযুক্তি রাতারাতি আবিষ্কৃত হয়নি, বরং ধীর গতিতে এর বিবর্তন ঘটেছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে ল্যান্ড ফোনের আবিষ্কার (১৮৭৬) যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটায়। এরপর বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাদা-কালো টেলিভিশন (১৯৩০-এর দশক) এবং ব্যক্তিগত কমপিউটারের (১৯৭০-এর দশক) আগমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নতুন করে সাজাতে শুরু করে। এরপর আসে ইন্টারনেট (১৯৮০-এর দশক) এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (১৯৯০-এর দশক) যা তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করে।
একুশ শতকের শুরুতে স্মার্টফোন (২০০৭) এবং ক্লাউড কম্পিউটিং-এর আবির্ভাব ব্যক্তিগত ও পেশাদার জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। বর্তমানে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং রোবটিক্স আমাদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। এই প্রবন্ধে, আমরা প্রযুক্তির এই ঐতিহাসিক বিবর্তন, এর ফলে সৃষ্ট সীমাবদ্ধতা, এবং আমাদের অর্থনীতি ও সমাজে এর বহুমুখী প্রভাব নিয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ করব।

প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষের অভিযোজন ও সীমাবদ্ধতা
প্রযুক্তি যখন ধাপে ধাপে এগিয়েছে, মানুষও তখন এর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এই যাত্রায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জও তৈরি হয়েছে। ল্যান্ড ফোন থেকে স্মার্টফোন, সাদা-কালো টিভি থেকে ডিজিটাল বিনোদন- এই পরিবর্তনগুলো মানুষের জীবনকে সহজ করলেও, এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে।
যোগাযোগের পরিবর্তন ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা: ল্যান্ড ফোনের যুগে যোগাযোগ ছিল সীমিত এবং ব্যয়বহুল। এরপর মোবাইল ফোন এলে মানুষ আরও সহজে যোগাযোগ করতে পারতো। কিন্তু স্মার্টফোন আসার পর মানুষ আর শুধু কথা বলে না, ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এর ফলে, যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা কমে এলেও, আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ঝুঁকির মুখে পড়ে। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে প্রায় ৫.৩ বিলিয়ন মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করে, যার ফলে অনলাইন ডেটা চুরির ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে।
সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: একসময় মানুষ একসঙ্গে বসে সাদা-কালো টিভি দেখত, যা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বাড়াতো। কিন্তু এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যেমন- নেটফ্লিক্স, ইউটিউব আসার পর মানুষ ব্যক্তিগতভাবে কন্টেন্ট দেখতে পছন্দ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, একজন গড়পড়তা প্রাপ্তবয়স্ক প্রতি বছর প্রায় ১৩০০ ঘণ্টা স্ট্রিমিং কন্টেন্ট দেখে, যা পারিবারিক মিথস্ক্রিয়া কমিয়ে দিচ্ছে। এই ভার্চুয়াল জগতের অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের বাস্তব জীবনের সামাজিক সম্পর্কগুলোকে দুর্বল করছে।
মানসিক চাপ এবং আসক্তি: নতুন প্রযুক্তি শেখার চাপ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মতো প্ল্যাটফর্মে অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করার প্রবণতা মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। সাইবার বুলিং এবং হারিয়ে যাওয়ার ভয় এর মতো সমস্যাগুলো মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। একইসঙ্গে, অতিরিক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে ঘুমের সমস্যা, চোখে চাপ পড়া এবং ‘টেক্সট নেক’-এর মতো শারীরিক সমস্যাও দেখা দিচ্ছে।
অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানে প্রযুক্তির প্রভাব
প্রযুক্তি শুধু আমাদের জীবনযাত্রাই নয়, অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের ওপরও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে একদিকে যেমন নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে, তেমনি পুরনও অনেক কাজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
শিল্প বিপ্লব এবং অটোমেশন: প্রথম শিল্প বিপ্লবের সময় বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং কারখানার যন্ত্রপাতি শ্রমিকের কাজ সহজ করেছিল। পরবর্তীতে কমপিউটার এবং রোবটিক্স অনেক পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ স্বয়ংক্রিয় করে দিয়েছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ৮০ কোটি মানুষের কাজ অটোমেশনের কারণে ঝুঁকিতে পড়বে। এটি বেকারত্বের ঝুঁকি বাড়ালেও, ডেটা সায়েন্স, এআই এবং সাইবার সিকিউরিটির মতো নতুন অনেক কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে।
ই-কমার্স এবং ডিজিটাল অর্থনীতি: আমাজন, আলিবাবার মতো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলো খুচরা ব্যবসা বদলে দিয়েছে। বৈশ্বিক ই-কমার্স বাজার বর্তমানে প্রায় ৫.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি। এর ফলে ছোট দোকানদাররা সমস্যার মুখে পড়লেও, অনেক নতুন অনলাইন ব্যবসা এবং ডেলিভারি সার্ভিস কোম্পানি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে উবার, এয়ারবিএনবি-র মতো প্ল্যাটফর্মগুলো ‘গিগ অর্থনীতির’ জন্ম দিয়েছে, যেখানে মানুষ নির্দিষ্ট কাজের জন্য চুক্তিতে কাজ করে। এর ফলে কর্মজীবনের স্বাধীনতা বাড়লেও, চাকরির নিরাপত্তা কমে যাচ্ছে।

প্রযুক্তি এবং সৃজনশীলতা
অনেক সময় মনে করা হয়, প্রযুক্তি মানুষের সৃজনশীলতাকে সীমিত করে। কারণ এখন যেকোনও সমস্যার সমাধান সহজেই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যদিকে, ডিজিটাল টুলস যেমন গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার, ভিডিও এডিটিং টুলস, বা মিউজিক প্রোডাকশন অ্যাপস মানুষের সৃজনশীলতাকে নতুন প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে। এই দ্বিমুখী আলোচনা প্রবন্ধে যোগ করা যেতে পারে।
সৃজনশীলতা এবং প্রযুক্তি: প্রযুক্তি মানুষের সৃজনশীলতাকে প্রভাবিত করে। এটি মানুষকে নতুন নতুন আইডিয়া এবং কৌশল শেখার সুযোগ করে দেয়।
প্রযুক্তি এবং গণতন্ত্র: আধুনিক সমাজে প্রযুক্তি, বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়া, গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তা আলোচনা করা যেতে পারে। কীভাবে প্রযুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচার এবং জনমত তৈরি করা হচ্ছে এবং একইসঙ্গে কীভাবে এটি সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করছে, তা তুলে ধরা যেতে পারে।
প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যসেবা: প্রবন্ধের বর্তমান সংস্করণে স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা আলোচনা থাকলেও, এর গভীরতা বাড়ানো যেতে পারে। কীভাবে প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত হচ্ছে, যেমন- টেলিমেডিসিন, স্বাস্থ্য অ্যাপস বা এআই-ভিত্তিক রোগ নির্ণয়, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য যোগ করা যেতে পারে।
প্রযুক্তি এবং শিক্ষা: শুধু ডিজিটাল সাক্ষরতা নয়, শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে এমনভাবে সাজানো যায়, যাতে শিক্ষার্থীরা দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, সেই বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এর জন্য সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যাথমেটিকস (এসটিইএম) শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা যেতে পারে।
ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের প্রস্তুতি
প্রযুক্তির এই দ্রুত পরিবর্তন আমাদের জন্য নতুন কিছু চ্যালেঞ্জও নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে নৈতিকতা, পরিবেশ এবং বৈষম্য।
নীতিমালা এবং আইন: প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কী ধরনের নতুন আইন বা নীতি তৈরি করা উচিত, সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। যেমন- ডেটা সুরক্ষা আইন, এআই-এর নৈতিক ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন।
নৈতিকতা ও এআই: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যত উন্নত হচ্ছে, ততই এর নৈতিক ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন ওঠছে। যেমন- একটি স্ব-চালিত গাড়ি যখন দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়, তখন এটি কার জীবন বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেবে। এআই-এর পক্ষপাতিত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বচ্ছতাও একটি বড় সমস্যা। ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রযুক্তি ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে হুমকির মুখে ফেলছে।
প্রযুক্তি এবং পরিবেশ: ডেটা সেন্টারগুলো প্রচুর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, যা কার্বন নিঃসরণ বাড়ায়। পাশাপাশি, পুরনও ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো (ই-বর্জ্য) পরিবেশের জন্য এক বড় হুমকি। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বিশ্বে প্রায় ৫৩.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন ই-বর্জ্য তৈরি হয়েছিল, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
ডিজিটাল বৈষম্য: প্রযুক্তির সুবিধাগুলো সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছায় না। শহুরে এবং গ্রামীণ এলাকার মধ্যে, ধনী এবং দরিদ্রদের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য স্পষ্ট। এটি একটি বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, যা দূর করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন।
মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে প্রযুক্তির সমন্বয়
প্রযুক্তি আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠেছে। এটি যেমন আমাদের জন্য অপার সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে, তেমনি এর চ্যালেঞ্জগুলোও কম নয়। মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো প্রযুক্তির সুবিধাগুলো গ্রহণ করা এবং এর ঝুঁকিগুলো মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা। এর জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কার করতে হবে, এসটিইএম শিক্ষার গুরুত্ব বাড়াতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ডিজিটাল ডেটক্স অনুশীলন করা এবং ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষায় সচেতন থাকা উচিত। সবশেষে, আমাদের মানবিক গুণাবলি, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক সম্পর্কগুলোকে রক্ষা করতে হবে, যাতে প্রযুক্তির এই যাত্রা আমাদের আরও উন্নত, মানবিক এবং সক্ষম একটি সমাজ গঠনে সহায়তা করে।
লেখক: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক মৃধা (সোহেল মৃধা)- প্রতিষ্ঠাতা কিনলে ডটকম, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ই-ক্যাব