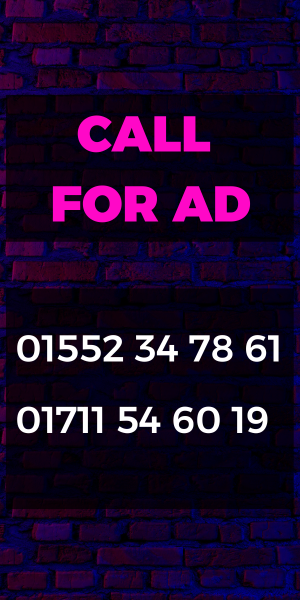অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে স্মার্ট প্রযুক্তির ছোঁয়া

ভূঁইয়া মোহাম্মদ ইমরাদ (তুষার) বাংলাদেশে অগ্নিকাণ্ড এখন ভয়াবহ এক দৈনন্দিন বিপর্যয়। রাজধানীর মার্কেট, গার্মেন্টস কারখানা, গুদাম, আবাসিক ভবন বা জাতীয় গুরুত্বপুর্ন স্থাপনা- সব জায়গাতেই হঠাৎ আগুন লেগে মুহূর্তের মধ্যে সর্বস্ব ছাই হয়ে যাচ্ছে। দেশের দমকল বাহিনীর সাহসী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আগুন নেভাতে দেরি হয়, কারণ অনেক সময় আগুনের উৎস দ্রুত শনাক্ত করা যায় না। অথচ আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে আগুন লাগার আগেই সতর্ক হওয়া এবং তা প্রতিরোধ করা সম্ভব- যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়।
স্মার্ট সেন্সর: আগুনের আগেই সংকেত
বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় এমন স্মার্ট স্মোক, গ্যাস ও তাপমাত্রা সেন্সর- যেগুলো ধোঁয়া, গ্যাস লিক বা অতিরিক্ত তাপমাত্রা শনাক্ত করলেই শব্দ, আলো ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সতর্কবার্তা পাঠায়। এই ডিভাইসগুলো খুব দ্রুত সাড়া দেয়, তাই আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই মানুষ নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারে বা দমকল বাহিনীকে খবর দেয়া সম্ভব হয়। একটি সাধারণ স্মোক সেন্সরের মূল্য ৮০০ থেকে ২,০০০ টাকার মধ্যে, তাই মধ্যবিত্ত পরিবার বা ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও সহজে ব্যবহার করা যায়।
থার্মাল ক্যামেরা ও ভিডিও নজরদারি
বড় ভবন, গুদাম বা শপিং মলে সাধারণ সেন্সর অনেক সময় কার্যকর হয় না, কারণ ধোঁয়া ওপরে না গিয়ে আটকে থাকে। এক্ষেত্রে থার্মাল ক্যামেরা তাপমাত্রার অস্বাভাবিক পরিবর্তন শনাক্ত করে দ্রুত সতর্কবার্তা দেয়।
ক্যামেরার ভিডিও বিশ্লেষণ সফটওয়্যার আগুনের উৎস কোথায় এবং কতটা ছড়িয়েছে তা নির্ধারণ করে ফায়ার সার্ভিসকে তাৎক্ষণিক তথ্য দেয়। বাংলাদেশের কিছু বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে এ ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার শুরু করেছে, যা ভবিষ্যতে অগ্নি নিরাপত্তায় বড় পরিবর্তন আনবে।
স্মার্ট স্প্রিংকলার ও অটোমেটেড নিবারণ ব্যবস্থা
আগে স্প্রিংকলার সিস্টেম শুধু পানি ছিটাতো, এখনকার স্মার্ট স্প্রিংকলার তাপমাত্রা ও ধোঁয়ার তথ্য বিশ্লেষণ করে কেবল বিপদজনক জায়গাতেই কাজ করে। এতে পানি নষ্ট হয় না এবং কার্যকারিতা বেড়ে যায়। এ ধরনের সিস্টেমকে ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করলে, সেন্সর, এলার্ম, ক্যামেরা ও স্প্রিংকলার- সবকিছু একই সিস্টেমে কাজ করে। ফলে আগুন লাগার মুহূর্তে মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই পুরো ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে পড়ে।
প্রশিক্ষণেও এসেছে ভার্চুয়াল প্রযুক্তি
আগুন লাগলে আতঙ্কে মানুষ প্রায়ই ভুল পথে দৌড়ায়। এ সমস্যা সমাধানে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) ও অগমেন্টেড রিয়েলিটি (AR) ভিত্তিক ফায়ার সিমুলেশন প্রশিক্ষণ। বাংলাদেশেও ফায়ার সার্ভিস ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে কর্মচারীরা আগুনের সময় সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবে, দমকলের অপেক্ষা না করেই প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারবে।
অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জায়গায় রয়েছে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। কিন্তু জনবল, সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত ঘাটতি এখনও তাদের বড় চ্যালেঞ্জ। একইসঙ্গে, সরকারের নীতি ও তদারকির ঘাটতিও বারবার বড় দুর্ঘটনা ডেকে আনছে। তাই এই দুই স্তর- ফায়ার সার্ভিস ও সরকার উভয়ের ভূমিকা সমন্বিত ও যুগোপযোগী হওয়া জরুরি।
বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিসের করণীয়: প্রযুক্তিনির্ভর ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
ফায়ার সেফটি কমান্ড সেন্টার: প্রতিটি জেলা ও শিল্পাঞ্চলে প্রযুক্তিনির্ভর ফায়ার সেফটি কমান্ড সেন্টার স্থাপন করা জরুরি। এই কেন্দ্রগুলো সেন্সর, ক্যামেরা ও থার্মাল ডিটেক্টর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সার্ভারে পাঠাবে। আগুন শনাক্ত হওয়া মাত্রই নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনে সতর্কবার্তা পৌঁছাবে, ফলে সাড়া দেয়ার সময় অর্ধেকে নেমে আসবে।
ড্রোন ও রোবট ইউনিট: বর্তমানে অনেক অগ্নিকাণ্ডই ঘন ধোঁয়া ও উঁচু ভবনে আটকে থাকা মানুষজনের কারণে জটিল হয়। ফায়ার সার্ভিসকে উন্নত ড্রোন ও রোবটিক ইউনিট ব্যবহার করতে হবে, যা দ্রুত তথ্য সংগ্রহ ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা করবে। বিশ্বের উন্নত শহরগুলো ইতিমধ্যে “ফায়ার রেসকিউ ড্রোন” ব্যবহার করছে। বাংলাদেশেও এটি চালু করা গেলে উদ্ধার দক্ষতা বহুগুণে বাড়বে।
ডিজিটাল প্রশিক্ষণ ও সিমুলেশন সেন্টার: আগুনের মতো বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ দিতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ও সিমুলেশন ল্যাব স্থাপন করা জরুরি। এতে নতুন সদস্যরা শুধু তত্ত্ব নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারবে। প্রতি বছর অন্তত একবার সব সদস্যের রিফ্রেশার ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করা উচিত।
জিপিএস ও রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং ব্যবস্থা: প্রতিটি ফায়ার ট্রাকে জিপিএস ডিভাইস স্থাপন ও একটি কেন্দ্রীয় রুট মনিটরিং সিস্টেম তৈরি করতে হবে। এতে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সময় ৩০–৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমে আসবে। একই সঙ্গে দুর্ঘটনাস্থলে রাস্তায় যানজট বা পানির অভাবের মতো সমস্যা আগেই চিহ্নিত করা যাবে।
স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটি ফায়ার টিম: প্রতিটি ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী কমিউনিটি ফায়ার ভলান্টিয়ার দল গঠন করা উচিত। এদের প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্ব ফায়ার সার্ভিস নিতে পারে। এতে ছোটখাটো আগুনের ঘটনায় স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সম্ভব হবে।
অগ্নি নিরাপত্তা অডিট: বাণিজ্যিক ভবন, গুদাম ও শিল্পকারখানাগুলোর জন্য বার্ষিক ফায়ার অডিট বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে লাইসেন্স নবায়ন হবে। ফায়ার সার্ভিসকে এ জন্য প্রযুক্তিভিত্তিক অডিট সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে, যাতে ঝুঁকি রেটিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়।
বাজেট ও আধুনিক সরঞ্জাম বৃদ্ধি: বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতি এক লাখ মানুষের জন্য ফায়ার সার্ভিস কর্মী সংখ্যা মাত্র ২০ জনের মতো। এ ঘাটতি কমাতে নতুন নিয়োগ ও উন্নত সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য আলাদা বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ জরুরি।
সরকারের করণীয়: নীতি, তদারকি ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ
জাতীয় ফায়ার নিরাপত্তা নীতি: একটি আপডেটেড “জাতীয় ফায়ার নিরাপত্তা নীতি” প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে নির্মাণ, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের জন্য নির্দিষ্ট নিরাপত্তা মান নির্ধারণ থাকবে।
নির্মাণ অনুমোদনে ফায়ার সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক: ভবনের নকশা অনুমোদনের সময় ফায়ার সেফটি ডিজাইন ছাড়া কোনও অনুমোদন দেয়া যাবে না। রাজউক, সিটি কর্পোরেশন ও ফায়ার সার্ভিসকে একটি যৌথ অনলাইন অনুমোদন প্ল্যাটফর্মে আনতে হবে।
জাতীয় ফায়ার ডেটাবেজ: দেশে বছরে গড়ে প্রায় ২৫ হাজার অগ্নিকাণ্ড ঘটে, কিন্তু কোনও সমন্বিত ডেটাবেজ নেই। একটি জাতীয় ফায়ার ডেটা সেন্টার স্থাপন করে অঞ্চলভিত্তিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।
প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রণোদনা: দেশীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে “ফায়ার সেফটি টেক ফান্ড” গঠন করা যেতে পারে, যেখানে সেন্সর, অ্যালার্ম ও স্প্রিংকলার ডিভাইস উৎপাদনে ট্যাক্স ছাড় ও আর্থিক সহায়তা থাকবে।
শিক্ষা ও সচেতনতা কর্মসূচি: প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে “অগ্নি নিরাপত্তা শিক্ষা” অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। একইসঙ্গে, টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে নিয়মিত ফায়ার সেফটি প্রচারণা চালু রাখতে হবে।
ফায়ার সিটি মডেল: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে পাইলট প্রকল্প হিসেবে “স্মার্ট ফায়ার সিটি” চালু করা যেতে পারে, যেখানে সেন্সর, ড্রোন, স্বয়ংক্রিয় স্প্রিংকলার ও কেন্দ্রীয় অ্যালার্ম সিস্টেম একসাথে কাজ করবে।
আইন প্রয়োগ ও তদারকি: অগ্নি নিরাপত্তা আইনে কঠোর জরিমানা ও কারাদণ্ড কার্যকর করতে হবে। নিয়মিত মনিটরিং টিম গঠন করে প্রতিটি বাজার, গুদাম ও কারখানা পরিদর্শনের রুটিন নির্ধারণ করতে হবে।
জরুরি সেবা সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম: ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, বিদ্যুৎ বিভাগ ও হাসপাতালের মধ্যে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য একটি ইউনিফায়েড কন্ট্রোল সেন্টার তৈরি করতে হবে। এটি হলে উদ্ধারকাজ ও চিকিৎসা সহায়তা অনেক দ্রুত হবে।
আগুন প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা
অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সরকারের নীতি, ফায়ার সার্ভিসের প্রযুক্তি বা আইনি কাঠামো যত শক্তিশালীই হোক না কেন, সাধারণ মানুষের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বেশিরভাগ অগ্নিকাণ্ডই ঘটে আমাদের অসতর্কতা, অবহেলা বা নিয়ম না মানার কারণে। দৈনন্দিন জীবনে কিছু সচেতন অভ্যাস গড়ে তুললেই আগুন লাগার ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। সচেতনতা, সতর্কতা আর দায়িত্ববোধেই কমবে দুর্ঘটনা।
গৃহস্থালী নিরাপত্তা ও বৈদ্যুতিক সতর্কতা: বাড়িঘর ও দোকানপাটে অগ্নিকাণ্ডের সবচেয়ে বড় কারণ হলো বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট। তাই ঘরে পুরনো বা ক্ষতিগ্রস্ত তার ব্যবহার না করা উচিত। একসঙ্গে অনেক যন্ত্রপাতি এক প্লাগে সংযুক্ত করা ঝুঁকিপূর্ণ। বৈদ্যুতিক লাইনের নিয়মিত পরিদর্শন করা জরুরি। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে ফ্যান, আয়রন, গ্যাসের চুলা ইত্যাদি বন্ধ আছে কি না তা দেখে নেয়া উচিত। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নিয়ম মানলে ঘরে আগুন লাগার ঝুঁকি অন্তত ৬০–৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব।
গ্যাস সংযোগ ও রান্নাঘরের নিরাপত্তা: বাংলাদেশে ঘরোয়া অগ্নিকাণ্ডের প্রায় অর্ধেকই গ্যাস লিকেজ থেকে ঘটে।
তাই রান্নাঘরে কিছু মৌলিক নিয়ম মেনে চলা জরুরি। রান্না শেষে গ্যাসের চুলা ও রেগুলেটর বন্ধ করতে হবে। গ্যাসের গন্ধ টের পেলে কখনও আগুন বা লাইট জ্বালানো যাবে না; দরজা–জানালা খুলে বাতাস চলাচলের সুযোগ দিতে হবে। রান্নাঘরে ছোট অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা অত্যন্ত কার্যকর। সিলিন্ডার স্থাপনের সময় সরাসরি সূর্যালোক বা তাপ থেকে দূরে রাখতে হবে।
বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকায় ব্যক্তিগত দায়িত্ব: যারা দোকান, গুদাম বা কারখানায় কাজ করেন, তাদেরও সচেতন হতে হবে। প্রতিটি কর্মীকে অগ্নি নিরাপত্তার মৌলিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কারখানায় জরুরি নির্গমনপথ সবসময় খোলা রাখতে হবে। দাহ্য পদার্থ (গ্যাস, কেমিক্যাল, তেল ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি মাসে একবার ‘ফায়ার ড্রিল’ আয়োজন করলে সবাই জানবে কীভাবে দ্রুত সরে যেতে হয়।
এলাকাভিত্তিক কমিউনিটি ফায়ার টিম: সাধারণ মানুষ চাইলে তাদের এলাকা বা পাড়া-মহল্লায় স্বেচ্ছাসেবী কমিউনিটি ফায়ার টিম গঠন করতে পারেন। ফায়ার সার্ভিস থেকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়ে এই দল স্থানীয় পর্যায়ে ছোটখাটো আগুন নেভাতে পারে। প্রতিটি কমিউনিটি ভবনের সামনে বা প্রধান রাস্তার পাশে পানির উৎস ও ফায়ার হাইড্রেন্ট চিহ্নিত রাখলে জরুরি পরিস্থিতিতে দমকলকর্মীরা দ্রুত কাজ করতে পারেন।
সচেতনতা গড়ে তোলা: অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো সচেতনতা। তাই বিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির, কমিউনিটি সেন্টার বা অফিসে ফায়ার সেফটি নিয়ে আলোচনা সভা বা প্রশিক্ষণ করা যেতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিরাপত্তা বিষয়ক ভিডিও বা বার্তা শেয়ার করা যেতে পারে। পরিবারে শিশুদের শেখাতে হবে গ্যাস লিকের গন্ধ পেলে কী করতে হবে বা আগুন লাগলে কোথায় ফোন করতে হবে (৯৯৯)।
দায়িত্বশীল নাগরিক আচরণ: অগ্নিনিরাপত্তা আইন ও বিধি মেনে চলা শুধু কর্তৃপক্ষের নয়, নাগরিকদেরও দায়িত্ব। যেমন- নির্মাণের সময় ফায়ার সেফটি ডিজাইন মানা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা। বাজার, অফিস, রেস্তোরাঁ বা ভবনে ফায়ার এক্সিট ও অ্যালার্ম আছে কি না দেখে সচেতন হওয়া। কোথাও বিপজ্জনকভাবে গ্যাস সিলিন্ডার বা তার জটলা দেখলে প্রশাসন বা ফায়ার সার্ভিসকে অবহিত করা।
আগুন লাগলে আতঙ্ক নয়, দ্রুত ব্যবস্থা: আগুন দেখলে প্রথমে আতঙ্কিত না হয়ে, দ্রুত ফায়ার সার্ভিসে ফোন করা (৯৯৯) এবং কাছাকাছি থাকা মানুষকে সতর্ক করা জরুরি। ছোট আগুনের ক্ষেত্রে পানি বা অগ্নিনির্বাপক ব্যবহার করা যায়, কিন্তু বড় আগুনে নিজের ঝুঁকি না নিয়ে সবাইকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে।
অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ কেবল আগুন নেভানোর বিষয় নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ “সিস্টেম রিফর্ম” প্রক্রিয়া। সরকারের সুপরিকল্পিত নীতি, ফায়ার সার্ভিসের প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ এবং নাগরিক সচেতনতা-এই তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে তৈরি হতে পারে একটি নিরাপদ ও আগুন-সহনশীল বাংলাদেশ। আগুন প্রতিরোধের জন্য শুধু দমকল নয়, প্রযুক্তি, সরকার, জনগণ সব পক্ষকেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। একটি ছোট সেন্সর, একটি থার্মাল ক্যামেরা কিংবা একটি ভিআর প্রশিক্ষণ এগুলোই হতে পারে শত প্রাণ বাঁচানোর উপায়। ডিজিটাল রুপান্তরের পথে এগোতে হলে “স্মার্ট অগ্নি নিরাপত্তা” এখন সময়ের দাবি। আজই সচেতন হই, প্রযুক্তিকে পাশে রাখি, নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ি।