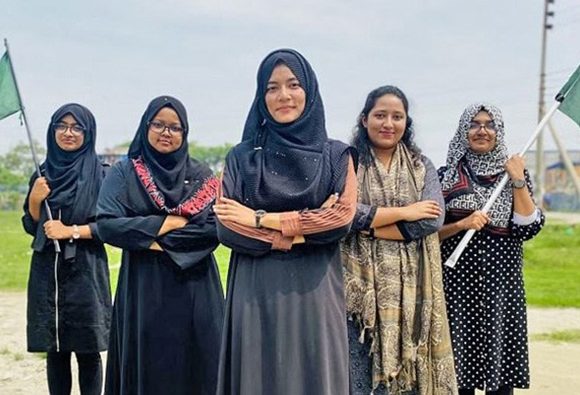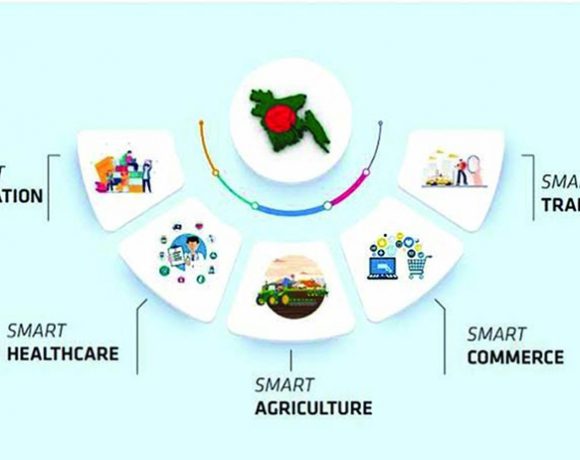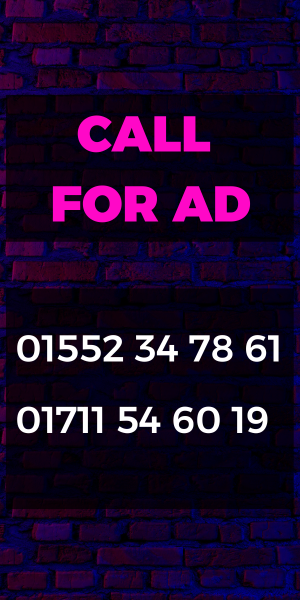স্বাধীন ইন্টারনেট নাকি নিয়ন্ত্রিত নেটওয়ার্ক?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক মৃধা (সোহেল মৃধা): বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ অধ্যাদেশ-২০২৫’-এর খসড়াটি দেশের ডিজিটাল শাসন কাঠামোয় এক দুই ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। একদিকে যেমন স্থায়ীভাবে ইন্টারনেট বন্ধের ওপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এবং ব্যাপক সমালোচিত ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) বিলুপ্তির মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
তেমনি অন্যদিকে ওভার-দ্য-টপ (ওটিটি) প্ল্যাটফর্ম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের কঠোর বিধান রেখে , ও স্বাধীনতার নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের পাশাপাশি, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনার প্রস্তাব ডিজিটাল অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের সদিচ্ছা নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এ যেন একদিকে স্বাধীনতার আশ্বাস, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণের অদৃশ্য জাল বিস্তারের চেষ্টা।
ইন্টারনেট বন্ধ অতীত? এনটিএমসি বিলুপ্তির স্বস্তি
খসড়া অধ্যাদেশের সবচেয়ে প্রশংসনীয় দিক হলো নাগরিকের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের অধিকার নিশ্চিত করা এবং ইন্টারনেট সংযোগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের অবসান। এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ‘‘টেলিযোগাযোগ সংযোগ, সংশ্লিষ্ট সেবা বা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস কোনও অবস্থাতেই বন্ধ, বিঘ্নিত বা সীমিত করা যাবে না।’’ এই বিধান দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। বিশ্বব্যাপী এক দিনে ইন্টারনেট বন্ধ থাকলে অর্থনীতিতে যে কয়েক মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়, যেমনটা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা বারবার দেখিয়েছে, তা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার পাশাপাশি ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং এবং এমএফএস নির্বিঘ্ন রাখবে।
আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো, অবৈধ নজরদারি ও গুমের অভিযোগে বারবার ব্যাপক সমালোচিত এনটিএমসি বিলুপ্তির প্রস্তাব। আইন প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, পূর্ববর্তী আইনের ৯৭ ধারার মাধ্যমে যে ব্যাপক বেসামরিক যোগাযোগের নজরদারি চালানো হতো, সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে শেষ করা হয়েছে।
আদালতের অনুমতিতেই নজরদারি: আইনগতভাবে প্রবেশ-এ সুরক্ষা কতটুকু?
এনটিএমসি বিলুপ্তির পর অধ্যাদেশে ‘আইনগতভাবে প্রবেশ’-এর ধারণা প্রবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে সামরিক বা নিরাপত্তা সংস্থা আদালতের অনুমতি ছাড়া কারও যোগাযোগে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ‘আইনগতভাবে প্রবেশ’ কেবল সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, সীমিত সময়ের জন্য এবং আদালত বা বিচারিক কাউন্সিলের পূর্বানুমোদনক্রমে করা যাবে। কল, বার্তা বা ইন্টারনেট ট্রাফিকের তথ্য কেবল অপরাধ তদন্ত, জীবন রক্ষা বা জাতীয় নিরাপত্তার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে, তবে কোনোভাবেই রাজনৈতিক বা আদর্শগত কারণে নয়।
তবে, বিশ্লেষকদের মতে, ‘জাতীয় নিরাপত্তা’র সংজ্ঞা দুর্বল বা অস্পষ্ট রাখা হলে রাজনৈতিক কারণে নজরদারির অপব্যবহারের ঝুঁকি থেকেই যাবে। এই ব্যবস্থার ফলে গণ-নজরদারি বন্ধ হবে এবং নাগরিকদের ব্যক্তিগত যোগাযোগের সুরক্ষা বাড়বে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিচারিক অনুমোদনসাপেক্ষে সংগৃহীত তথ্যই কেবল আদালতে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে, অনুমতি ছাড়া সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্য আদালতে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে না।
বেআইনিভাবে আড়ি পাতার মতো অপরাধের জন্য ২ বছরের কারাদণ্ড বা দেড় কোটি টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে, যা নিয়মবহির্ভূত নজরদারির ক্ষেত্রে কঠোরতা নিশ্চিত করে। এ ছাড়াও, ফোনে অশ্লীল/অশোভন বার্তা পাঠালে ধারা ৬৯ অনুযায়ী অনধিক দুই বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক দেড় কোটি টাকা অর্থদণ্ড এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে বারবার ফোন করে বিরক্ত করলে ধারা ৭০ অনুযায়ী এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড হতে পারে।
ওটিটি-কে কড়া শর্ত: সামাজিক মাধ্যম কি তবে নতুন নজরদারির কেন্দ্র?
খসড়া অধ্যাদেশের সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ হলো ওভার-দ্য-টপ (ওটিটি) প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন মেসেজিং এবং ভিডিও স্ট্রিমিং অ্যাপসগুলোকে সরকারের অনুমোদনের আওতায় আনার প্রস্তাব। ওটিটি বলতে নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও, ইউটিউব, সেই সঙ্গে দেশীয় প্ল্যাটফর্ম যেমন চরকি, হইচই, এবং মেসেজিং অ্যাপ যেমন হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রামও বোঝানো হতে পারে। এসব সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানকে এখন থেকে বাংলাদেশে নিবন্ধন নিতে হবে এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তা সংস্থাকে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, ইন্টারনেট বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলেও খসড়ায় একটি ব্যতিক্রমী বিধান রাখা হয়েছে, তা হলো- রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে সরকার প্রয়োজনে যেকোনও প্ল্যাটফর্ম স্থগিত বা বন্ধ করতে পারবে। সমালোচকরা আশঙ্কা করছেন, এই ধারাটি একটি ‘পেছনের দরজা’ হিসেবে কাজ করতে পারে এবং জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।
চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা
এই খাতে একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে ‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কমিশন’ গঠিত হবে, যা লাইসেন্স প্রদান, নীতিনির্ধারণ ও স্পেকট্রাম বণ্টনের দায়িত্বে থাকবে। এই কমিশন পাঁচ সদস্যের হবে। তবে, কমিশনে সরকারি হস্তক্ষেপ এড়াতে এবং এর পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট বিধান জরুরি। এই আইন কার্যকর হলে আইএসপি বা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি)-এর অন্তর্ভুক্ত আইএসপিগুলোর জন্য ব্যবসা পরিচালনায় অনিশ্চয়তা কমবে এবং গ্রাহকরা নিরবচ্ছিন্ন সেবা পাবে।
তবে নতুন আইনের মূল চ্যালেঞ্জ হলো এর বাস্তবায়ন ও অপব্যবহার রোধ করা। বিশেষজ্ঞরা ‘আইনগতভাবে প্রবেশ’-এর সংজ্ঞা আরও স্পষ্ট করে প্রতিটি প্রবেশের জন্য আদালতের অনুমতি বাধ্যতামূলক করার দাবি তুলেছেন।
১০২ ধারাবিশিষ্ট এই খসড়া অধ্যাদেশটি ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত জনমতের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই আইন চূড়ান্ত রূপ নেয়ার সময়, এর মাধ্যমে যেন নাগরিকদের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের অধিকার নিশ্চিত হয় এবং একইসঙ্গে নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণের সুযোগগুলো যেন কঠোর বিচারিক তদারকির আওতায় থাকে, তা নিশ্চিত করা জরুরি। অন্যথায়, ইন্টারনেট স্বাধীনতার প্রচ্ছদে লুকিয়ে থাকা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেশের ডিজিটাল ভবিষ্যতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠবে। তাই নাগরিক সমাজ ও অংশীজনদের দাবি, এই অধ্যাদেশ যেন শুধু নজরদারির নয়, বরং ডিজিটাল অধিকার রক্ষার দলিল হয়ে ওঠে।