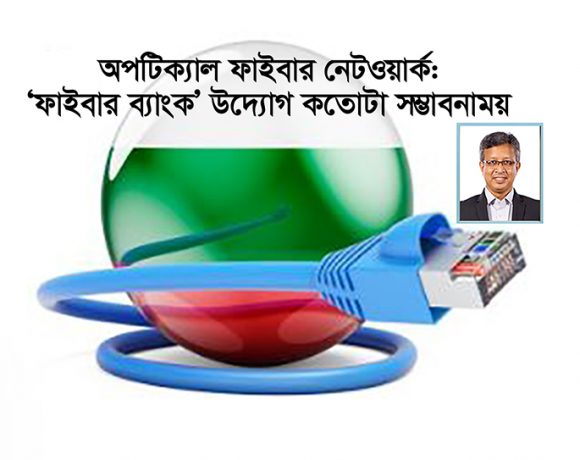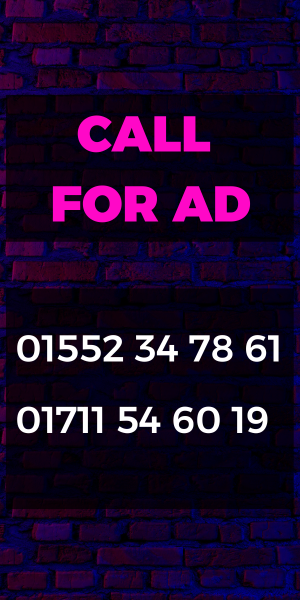ব্রডব্যান্ড যুদ্ধ: সংকটের মুখে বাংলাদেশের আইএসপি খাত

মোহাম্মদ আমিনুল হাকিম: বাংলাদেশে ইন্টারনেট বিপ্লবের সূচনা হয় আইএসপিদের (ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার) হাত ধরে, যারা ঘরে ঘরে ব্রডব্যান্ড পৌঁছে দিয়েছে। এই আইএসপিরা (আইএসপি কর্মীরা) দেশের প্রতিটি অলিতে-গলিতে ফাইবার টেনে, শত বাধা পেরিয়ে, ডিজিটাল কানেক্টিভিটির ভিত গড়ে তুলেছে। আজ যখন মোবাইল অপারেটর ও আন্তর্জাতিক প্লেয়াররা দেশের বাজারে আরও গভীরভাবে ঢুকছে, তখন আমাদের এই পুরনও যোদ্ধারা এক ধরনের অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে।
আমরা যদি একটু পেছনে তাকাই, তাহলে বুঝতে পারবো এই আইএসপিরাই তো বাংলাদেশের হাজারও তরুণকে প্রথমবারের মতো ইউটিউব, ফেসবুক চিনিয়েছে, ফ্রিল্যান্সিং শিখতে সাহায্য করেছে। এই খাতের অবদান মোটেই মূল্যহীন নয়, বরং জাতিগত অগ্রগতির অংশ। তবুও সময় থেমে থাকে না। প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলে, যেকোনও খাতেই ধাক্কা আসে। আজ সেই বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়েছে আইএসপি খাত।
আইএসপির ইতিহাস ও অপরিসীম অবদান
একুশ শতকের শুরুর দিকে যখন ব্রডব্যান্ড শব্দটিই ছিল নতুন, তখন একদল তরুণ উদ্যোক্তা ও টেক-উদ্যোমীরা ঢাকার অলিগলি, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে হাতে বানানো নেটওয়ার্ক দিয়ে ইন্টারনেট সেবা সরবরাহ শুরু করেন। কেউ পুঁজি পেয়েছিলেন পরিবারের কাছ থেকে, কেউ ধার করে কিন্তু একটি অভিন্ন স্বপ্ন ছিল সবার, মানুষকে যুক্ত করতে হবে জ্ঞানের সঙ্গে। এই আইএসপিরাই প্রথম গ্রাহকের দরজায় গিয়ে ফাইবার ক্যাবল লাগিয়েছেন, রাত ৩টায় ডাউন টাইমে দৌড়ে গিয়েছেন লাইন ঠিক করতে। হাজারও ফ্রিল্যান্সার, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবীকে দিয়েছেন নির্ভরযোগ্য সংযোগ।
বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে; যখন পুরো দেশ থেমে গিয়েছিল, তখন এই আইএসপি কর্মীরা ঘরে বসে মানুষ যাতে কাজ করতে পারেন, পড়াশোনা ও ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন- সেই লাইফলাইন হিসেবে কাজ করেছেন। সরকার-প্রণীত ডিজিটাল সেবা, টেলিমেডিসিন, অনলাইন শিক্ষা এবং হোম অফিস তথা রিমোট ওয়ার্কিং সবই সম্ভব হয়েছে এই খাতের নীরব, কিন্তু অপরিহার্য অবদানে।
আইএসপি খাতের সামনের চ্যালেঞ্জ
বাংলাদেশের টেলিকম খাতে বড় একটা পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি সম্প্রতি যে খসড়া নীতিমালা প্রকাশ করেছে, তাতে মোবাইল অপারেটরদের এখন থেকে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গ্রাহকদের জন্য তারযুক্ত ব্রডব্যান্ড সেবা দেয়ার অনুমতি দেয়া হতে পারে।
(7.3.2 They will use designated radio frequency to connect the end users. But at the same time, when technology allows, and the solutions demand they can also combine both radio and wired access technologies to provide enterprise solutions.) যা হবে দেশীয় উদ্যোক্তাদের মেরে ফেলার প্রথম উদ্যোগ।
এমএনওরা (মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর) ইতিমধ্যে মোবাইল ডেটা, ফিক্সড ওয়্যারলেস একসেস (এফডাব্লিউএ) সেবা দেয়ার অনুমতি পেয়েছে। যা দিয়ে মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘরে-ঘরে ব্রডব্যান্ড সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। এখানেই শেষ নয় স্টারলিংকের মতো আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট-নির্ভর ইন্টারনেট সেবা খুব শিগগিরই বাংলাদেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। ফলে, ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা হবে শুধু দাম বা গতিতে নয়, বরং অভিজ্ঞতা, গ্রাহকসেবা ও প্রযুক্তিতে কে কতটা দক্ষ তার ওপর নির্ভর করে। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের আইএসপিগুলোর সামনে এখন অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন।
কেন এই অবস্থা তৈরি হলো?
সমাজের একটা বড় অংশ দোষারোপ করছে আইএসপিদেরকে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহকরা অভিযোগ করে আসছেন নিম্নমানের পরিষেবা, নিয়মিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া, দ্রুত সাপোর্ট না পাওয়া, ঝুলন্ত তার এবং স্বচ্ছ প্যাকেজিং ও বিলিং সিস্টেমের অভাব ইত্যাদি বিষয়কে। অনেক আইএসপি টেকনোলজিতে বিনিয়োগ না করে শুধুই ব্যবসা বাড়ানোর পেছনে ছুটেছে।
কিন্তু আইএসপি ব্যবসায়ীদের অনুসন্ধান বলছে আরও কিছু বিষয় রয়েছে, যেমন- ইন্টারনেট ইকো সিস্টেমে প্রতিটি লেয়ারে ভ্যাট, উচ্চকর, উচ্চ রেভিনিউ শেয়ারিং হার, সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (এসওএফ), অ্যাকটিভ শেয়ারিংয়ের অনুমতি না দেয়া, পেশি শক্তির ব্যবহার, অবৈধ লাইসেন্সধারীদের উৎপাত। এসব কারণেও এই খাতে একটা অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। আইএসপি ব্যবসায়ীরা এসব নিয়ে বেশি চাপে রয়েছেন। ফলে এক ধরনের নাজুক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই খাতে। বিগত বছরগুলোতে ফ্যাসিস্ট সরকার কখনোই উল্লেখিত সমস্যাগুলো সমাধানে কোনও ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এখন আমাদের দেখার বিষয়, এই সমস্যাগুলো বর্তমান সরকার কবে নিরসন করে। নাকি আদৌ করবে না?
আইএসপি খাতের মূল শক্তি কোথায়?
যদিও চ্যালেঞ্জ বাড়ছে, তবুও বাংলাদেশের আইএসপিগুলোর অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে, যেগুলোর ভিত্তিতে তারা এখনও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে এবং আগামীতে এগিয়ে যেতে পারে। যেমন…
লোকাল কমিউনিটির সঙ্গে গভীর সংযোগ: আইএসপিরা স্থানীয় লোকজন, স্থানীয় মার্কেট ও প্রয়োজন সম্পর্কে ভালোভাবে জানে।
দ্রুত রেসপন্স: মোবাইল কোম্পানিগুলো যেখানে টিকিট সিস্টেমে (সমস্যা সমাধানের জন্য দেয়া নম্বর) এক সপ্তাহ সময় নেয়, সেখানে আইএসপির একজন ফিল্ড টেকনিশিয়ান একটি ফোন কল পেয়ে ৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হন। এটি শুধু সার্ভিস নয়, এটি সম্পর্ক।
সাধ্যের মধ্যে মান: আজও দেশের সবচেয়ে কম খরচে আনলিমিটেড ব্রডব্যান্ড সেবা দিচ্ছে আইএসপিরা। যেখানে ৫০০ টাকায় ১০ থেকে ১৫ এমবিপিএস গতি পাওয়া যায়, যা বিশ্বের দরিদ্র দেশের মানদণ্ডেও প্রশংসাযোগ্য।
নির্ভরযোগ্যতা: অনেক ক্ষেত্রে লোকাল ফাইবারের মাধ্যমে আইএসপিরা নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিতে পারে, যেখানে মোবাইল ডেটা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।
গ্রাহকের আস্থা: যে পরিবারে ৮ বছর ধরে একই আইএসপি সেবা দিচ্ছে সেখানে নতুন এমএনও এলেও মানুষ ভাবে- ওদের ছেলে তো গত মাসে এসেছিলো, খুব ভালো সার্ভিস দেয়। এই ধরনের ব্র্যান্ড লয়্যালিটি তৈরি করতে বছরের পর বছর লাগে।
আইএসপিদের করণীয়: বাঁচতে হলে বদলাতে হবে
এখন প্রশ্ন হলো, আইএসপি খাত কি শেষ হয়ে যাচ্ছে? উত্তর হলো- না। শুধু যদি তারা নিজেদের দ্রুত বদলাতে পারে। তাহলে তারা টিকে থাকবে এবং তা বেশ ভালোভাবেই। পরিবর্তিত বাস্তবতায় টিকে থাকতে হলে নিচের দিক-নির্দেশনাগুলো প্রতিপালন করা জরুরি…
সেবার মান উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে: আইএসপিদের এখন লো কস্ট, লো কোয়ালিটি মডেল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানসম্মত ব্যাকহল, শক্তিশালী ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক, রিডানডেন্সি এবং সক্রিয় মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এরজন্য টেকনোলজিতে বিনিয়োগ জরুরি।
গ্রাহকসেবার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে: অনেক আইএসপি এখনও গ্রাহক সেবা বলতে বোঝে- কল করলেই কাউকে পাঠিয়ে দাও। এই মানসিকতা বদলাতে হবে। এখন সময় এসেছে পেশাদার গ্রাহকসেবা চালু করার। ২৪/৭ কাস্টমার কেয়ার, স্মার্ট টিকেটিং সিস্টেম, লাইভ চ্যাট এবং অটোমেটেড সাপোর্ট টুল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।
প্রযুক্তি ও সফটওয়্যারে দক্ষতা অর্জন করতে হবে: আইএসপিদেরও নিজস্ব সিআরএম, এনএমএস, বিলিং সিস্টেম এবং রিয়েল টাইম অ্যালার্টিং প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে হবে।
জোটবদ্ধ হয়ে নীতিমালার সংস্কারে অংশ নিতে হবে: আইএসপি ফোরাম, ব্রডব্যান্ড সংগঠন এবং খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্ল্যাটফর্মকে আরও সক্রিয় হতে হবে। নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে যাতে এমএনও ও আইএসপির জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত হয়।
ডিজিটাল লিটারেসি ও কমিউনিটি এনগেজমেন্ট: আইএসপিরা চাইলে নিজেদের এলাকাভিত্তিক কমিউনিটি গড়ে তুলতে পারে- যেখানে স্থানীয় ইন্টারনেট ইভেন্ট, সচেতনতামূলক কার্যক্রম বা স্কুলে ডিজিটাল লিটারেসি প্রোগ্রাম চালু করে নিজেদের উপস্থিতি ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব।
নতুন বাজারে আগ্রহী হোন: ঢাকায় প্রতিযোগিতা তীব্র হলেও গ্রামীণ অঞ্চল ও ছোট শহরগুলোতে এখনও বড় সম্ভাবনা রয়েছে। আইএসপিরা চাইলে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।
বিকল্প সেবা চালু করা: আইএসপি মানে শুধু ইন্টারনেট নয়- তার সাথে থাকতে পারে আইপি ফোন, আইপি টিভি, ক্লাউড স্টোরেজ, লোকাল সিডিএন ইত্যাদি। এটি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক গভীর করে।
সরকারের করণীয়: দেশীয় উদ্যোক্তাদের বাঁচাতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।
গত ১৯ এপ্রিল (২০২৫) আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন ৫০০ টাকায় ৫ এমবিপিএস গতির পরিবর্তে ১০ এমবিপিএসের ঘোষণা দেয়। তারই ফলশ্রুতিতে ফাইবার অ্যাট হোম সর্বপ্রথম ২১ এপ্রিল (২০২৫) আইআইজি লেয়ার থেকে ১০ শতাংশ এবং এনটিটিএন লেয়ারে ১৫ শতাংশ মূল্যছাড়ের ঘোষণা দেয়। পরবর্তী সময়ে সামিট কমিউনিকেশনস লিমিটেড ২২ এপ্রিল (২০২৫) ইন্টারনেটে ১০ শতাংশ এবং এনটিটিএনে ১৫-২০ শতাংশ মূল্যছাড়ের ঘোষণা দেয়। বাহন লিমিটেড এনটিটিএনে ১০ শতাংশ মূল্যছাড়ের ঘোষণা দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আইএসপি ইন্ডাস্ট্রি ছাড়া আর কেউ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেনি তথা এখনও মূল্যছাড় বাস্তবায়ন করেনি। সরকারকেই এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে বলে আমি মনে করি।
ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অ্যাকটিভ শেয়ারিংয়ের অনুমতি প্রদান করতে হবে। ইন্টারনেট সেবাকে আইটি এনাবল সার্ভিস হিসাবে ঘোষণা দিতে হবে। ইন্টারনেট সেবার ওপর থেকে সরকারকে রেভিনিউ শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (আইএসপি) থেকে সোশ্যাল অবলিগেশন ফান্ড (এসওএফ) আদায় বন্ধ করতে হবে।
এখানেই শেষ নয়, এটা একটা নতুন শুরু
আইএসপি খাত এখন কঠিন সময় পার করছে। কিন্তু যে খাত ঘরে ঘরে ইন্টারনেট পৌঁছে দিয়ে এক সময় দেশকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশে রূপান্তর করেছে, তারা হারিয়ে যাবে এটা সহজে মানা যায় না। বরং এই চ্যালেঞ্জটিকে নতুন করে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত। আইএসপিদের আছে অভিজ্ঞতা, লোকাল জ্ঞান, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং গ্রাহকদের আস্থা। এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই আইএসপিরা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে। এখন প্রশ্ন একটাই- সরকার কি দেশীয় উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়াবে?
লেখক: আমিনুল হাকিম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আম্বার আইটি লিমিটেড এবং চেয়ারপার্সন- বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম (বিআইজিএফ)।
কৃতজ্ঞতায়: ইনফো টেক ইনসাইট